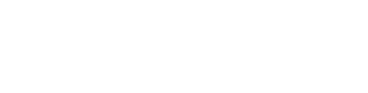একবিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডিগুলোর একটি হলো আত্মপরিচয় সংকট বা আইডেন্টিটি ক্রাইসিস। আত্মপরিচয় সংকট তখন ঘটে, যখন একজন ব্যক্তি তার অস্তিত্বের কারণ সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে যায়। তার অস্তিত্ব ব্যাখ্যা করার মতো যথোপযুক্ত কোনো কারণ খুঁজে পায় না। তার জীবনের উদ্দেশ্য ও গন্তব্য তার নিকট অস্পষ্ট থাকে। একসময় গিয়ে মনে হয়, এই বেঁচে থাকাটা অনর্থক; তার বেঁচে থাকা বা না থাকার সাথে দুনিয়ার কারো কিছু যায় আসে না।
যে মূল্যবোধগুলো কয়েকশ বছর ধরে আমাদের সমাজ গঠন করেছে, এর ব্যাপারে আমাদেরকে সন্দিহান করা তোলা হয়েছে। বরং ঐ বিষয়গুলোকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে, যা আমাদের সমাজে কখনো গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়নি।
আমাদের সমাজে দেখা যাচ্ছে, যখন একজন মানুষের আইডেন্টিটি ক্রাইসিস শুরু হয়, তখন সে তার নিজের ভাষা বলতে লজ্জাবোধ করে। নিজের সমাজের মূল্যবোধের সাথে নিজেকে যুক্ত করতে চায় না। নিজের পিতা-মাতার ব্যাপারে গর্বিত হতে পারে না। আবহমানকাল থেকে আমাদের সমাজে নিজের দেশ ও ধর্মের প্রতি মানুষের যে সম্পর্ক ও টান আছে, সেই টান ও সম্পর্ককে অনুভব করতে অসমর্থ হয়। সম্পর্ক তখন ধীরে ধীরে মূল্যহীন হয়ে পড়ে। সম্পর্কের মানদণ্ড হয়ে পড়ে টাকা। এই টাকা বা সম্পদই নির্ধারণ করে সে কি নিজ দেশে থাকবে যেখানে তার বাবা-দাদারা সারা জীবন কাটিয়েছেন, না-কি নিজের ভবিষ্যৎ চিন্তায় চলে যাবে ঠাণ্ডা কোনো দেশে যার পাসপোর্টের মূল্য বেশি। নিজ দেশ যেখানে আযান শুনতে কোনো কষ্ট করতে হয় না, মসজিদ খুঁজতে দূরে যেতে হয় না, পরিচিত মানুষ খুঁজতে গলির বাইরে ঘোরা লাগে না, সে সব ছেড়ে একসময় চলে যাওয়ার চিন্তা শুরু হয়।
আইডেন্টিটি ক্রাইসিসের স্থান মনোজগৎ। আমাদের সময়ে জীবনের একেক পর্যায়ে প্রত্যেক ছেলেমেয়ের মনে তিনটি প্রশ্নের উদ্ভব হয়, যা অধিকাংশ ক্ষেত্রে তার মনোজগতকে নিয়ন্ত্রণ করে। আমাদের সন্তানদের মনস্তত্ত্ব এবং আমাদের নিজেদের মনস্তত্ত্বের ওপর এই তিন প্রশ্নের প্রভাব কল্পনাতীত।
প্রথম প্রশ্নটি একটি শিশুর জীবনের প্রথম ১০ বছর তার মনোজগতকে ব্যস্ত রাখে এবং আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে। ১০ বছর পরে বাকি দুইটি প্রশ্ন তার মনে উদ্ভব হয়। এই প্রশ্নগুলো কীভাবে তার মনে প্রভাব ফেলবে এবং কত দিন ধরে তাকে কুরে কুরে খাবে, এটা নির্ভর করে সে তার পরিবারের কাছ থেকে কী রকম শিক্ষা পেয়েছে, তার ওপর। যদি আমরা তাদের ভালোভাবে প্রতিপালন করতে পারি, তাহলে তার মনে এই প্রশ্নগুলো ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে অস্তিত্বহীন হতে থাকবে। যদি দ্বীনের বুঝ ছোটবেলা থেকেই পেতে থাকে, তবেই একজন ব্যক্তি নিজেকে এই প্রশ্নগুলোর বেড়াজাল থেকে উদ্ধার করতে সক্ষম হয়।
শিশুর মনোজগৎ গঠনের শুরুতেই প্রথম মনস্তাত্ত্বিক প্রশ্ন তার মাথায় আসে, ‘আমার প্রতি কি মনোযোগ দেওয়া হচ্ছে?’ (Am I being noticed or not?)
সে তার পছন্দের খেলনাটি ছেড়ে উঠে যায়, এর কারণ আমি বাবা হয়ে তার প্রতি লক্ষ করছিলাম না। সে তার পছন্দের গল্পটি পড়তে পড়তে ছেড়ে দেয়, কারণ আমি মা তাকে রেখে অন্য কাজে ব্যস্ত হয়ে গিয়েছি। সে চায় সে ওই বইটি পড়বে, কিন্তু আমিও যেন তার সামনে বসা থাকি। সে চায় তার দিকে লক্ষ্য রাখা হোক।
এই সমস্যা তার জীবনের প্রথম ১০ বছরে হয়। যে সন্তান তার পিতা-মাতার কাছ থেকে যথেষ্ট মনোযোগ পায় এবং ভালো শিক্ষা পায়, সে খুব তাড়াতাড়ি এই প্রশ্নের হাতকড়া থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিতে পারে। কিন্তু যদি পরিবার থেকে ভালো শিক্ষাটা না পায়, তাহলে সম্ভাবনা থাকে যে ৪৫ বছর বয়সে এসেও সে সন্তান এই প্রশ্ন থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারছে না। এমনও ঘটনা আছে, সেনাবাহিনীর কর্নেল হয়ে গেছে, এখনও একই সমস্যায় জর্জরিত— বাবা আমার প্রতি খেয়াল রাখে কি রাখে না (The need of attention from the parents)।
বাকি প্রশ্ন দুইটি বয়ঃসন্ধির কিছু আগে তার মনোজগতে ঢুকে এবং তার চিন্তাকে সম্পূর্ণ নিজের কব্জায় নিয়ে চলে আসার চেষ্টা করে।
দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো : ‘আমাকে কেমন দেখাচ্ছে?’ (How am I looking?)
সন্তানকে মাদরাসায় পাঠনো হোক কিংবা স্কুলে, আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে বারবার নিজেকে দেখা তার মনস্তাত্ত্বিক চাহিদায় পরিণত হয়। সে এটা নিয়ে সবসময় চিন্তিত থাকে, তাকে কেমন দেখাচ্ছে, মানুষের কাছে তার নিজের উপস্থাপনটা (presentation) কেমন হচ্ছে। সে এই সময় একটি পর্বে প্রবেশ করে যাকে আমরা বলতে পারি তীব্র আত্মসচেতনতা পর্ব (Hightened self-consciousness)।
যখন সে প্রকৃত শিক্ষা পাবে (দ্বীনের শিক্ষা, প্রচলিত নষ্ট শিক্ষাব্যবস্থার শিক্ষা নয়) এবং তার সাথে পারিবারিক মূল্যবোধের একটি দৃঢ় ভিত্তি থাকবে, এই প্রশ্নের থাবা থেকে সে নিজেকে অনেকখানি মুক্ত করতে পারবে। তবে এই প্রশ্ন ধীরে ধীরে অবদমিত হবে কিন্তু পুরোপুরি চলে যাবে না। এ ব্যক্তি নিজের ভূষণ (Look) নিয়ে অযথা মাথা ঘামাবে না। তবে সমাজে চলার খাতিরে সে গ্রহণযোগ্য একটি ড্রেসকোডও মেনে চলবে না।
এর বিপরীতে আছে সে সকল সন্তান, যারা বাবার কাছে জিদ ধরবে, আমাকে অমুক ব্র্যান্ডেরই কাপড় কিনে দিতে হবে। এর কমে সে কখনো রাজি হতে চাইবে না। তার পিতাও এই চিন্তায় মশগূল থাকে আমি শুধু উমুক ব্র্যান্ডের কাপড় ও জুতা পরব। বাচ্চাদের এই মানসিকতা বড় হবার পরও আমাদের মধ্যে থেকে গেছে।
দ্বিতীয় প্রশ্নের সমাধান হতে না হতেই জীবনে তৃতীয় প্রশ্নের আগমন ঘটে।
‘আমার ব্যাপারে আমার বন্ধুমহল ও পরিচিতরা কী ভাবে?’ (What do my peers think about me?)
এখানে সহজীকরণের স্বার্থে আমরা বলতে পারি, peer বলতে বোঝায় সেই সব ব্যক্তি, যাদেরকে আমি নিজের ক্লাবে শামিল করি। জিনিসটি আরেকটু ব্যাখ্যা করলে হয়তো বুঝতে সুবিধা হবে। একজন ব্যক্তি সমাজের প্রত্যেকের সাথে নিজেকে সম্পর্কযুক্ত মনে করে না এবং তাদের সাথে নিজেকে তুলনা করে। তার মনোজগতে অবচেতনভাবে একটি ক্লাব গঠন করে এবং সে ওই ক্লাবের চিরস্থায়ী সদস্য। এ ক্লাবের অন্য সদস্যদের সে অবচেতনভাবেই ক্লাবে শামিল করে এবং এই ক্লাবে তার নিজের সামাজিক অবস্থান সব সময় যাচাই করতে থাকে। সে নিজে ছাড়া অন্য সদস্যরা সময় ও অন্যান্য পারিপার্শ্বিকের প্রভাবে পরিবর্তিত হয়। শুরুর দিকে এই ক্লাবের সদস্য থাকে স্কুলের ক্লাসমেট, সমবয়সী কাজিন এবং এলাকার বন্ধুবান্ধব। একটু বয়স হলে সেই ক্লাবে পুরনো সদস্যদের স্থলে যুক্ত হয় তার অফিসের কলিগ, তার ব্যাচের বন্ধুবান্ধব, গৃহিণীদের ক্ষেত্রে পাশের ফ্লাটের ভাবি ইত্যাদি।
কিশোর বা তরুণদের ক্ষেত্রে এই এক্সক্লুসিভ ক্লাবের সদস্যদের সাথে তাদের মানসিক সম্পর্কের বিষয়টা অনেকটা স্ত্রীর সাথে তার বাবার বাড়ির সম্পর্কের মতো। একজন স্ত্রী কখনোই তার স্বামীর মুখ থেকে নিজ পরিবার সম্পর্কে খারাপ কথা মেনে নিতে পারে না। যদি আপনি বলেন যে কালকে থেকে তুমি অমুক ছেলেটার সাথে মিশবে না, সে ভালো না; দেখা যায়, সে তার সাথে মেশা বন্ধ করে দেয় না। সে শুধু এটা শিখে যে পিতা-মাতার সামনে সেই বন্ধুর নাম আর উচ্চারণ করা যাবে না। আর আপনি যদি খুব বেশি চাপ দেন, তাহলে সম্পর্ক আপনাদের ভেতরে খারাপ হবে, কিন্তু ওই বন্ধুর সাথে আপনার সন্তানের সম্পর্ক খারাপ হবে না।
ওপরের তিনটা প্রশ্ন একজন ব্যক্তির মনস্তাত্ত্বিক চরিত্রকে নিয়ন্ত্রণ করে। একবিংশ শতাব্দীর ‘সফলতা’ মানুষকে ওই সব প্রশ্ন থেকে আলাদা করে ফেলেছে যা তার উদ্দেশ্যকে ব্যাখ্যা করে। আর যে সকল বিষয় নিতান্তই তুচ্ছ এবং অপ্রয়োজনীয়, সেই সকল প্রশ্নের গোলকধাঁধায় আমাদের ফেলে দেওয়া হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত বিদ্যা শিখলে বাহবা দেওয়া হলেও ভবিষ্যতের মায়েদের নিকট তারবিয়াত বা সন্তান প্রতিপালন শেখার বিষয়টিকে অপমানজনক হিসেবে তুলে ধরা হচ্ছে। সন্তানকে উত্তম শিক্ষা দেওয়া এবং সঠিকভাবে প্রতিপালন করা, এটাও শেখার বিষয় এবং এটা একটা আর্ট। এর জন্য বাচ্চার মনস্তত্ত্ব বুঝতে হবে, তবে সবার আগে আমাদের নিজেদের উপরে কিছু কাজ করতে হবে।
বুঝতে হবে সাফল্য কী? মহান সৃষ্টিকর্তার চোখে কে সফল? বিশ্বের ৭০০ কোটি মানুষ আমাকে সফলতার ভিন্ন সংজ্ঞা শেখাতে চাইলেও আমি সেটা দ্বারা বিভ্রান্ত না হয়ে আমি সেই বিষয়ে সফলতা খুঁজব তাঁর বিধানের আলোকে, যার উপর আমি ঈমান এনেছি। এর জন্য সন্তানের সাথে সময় ব্যয় করতে হবে এবং ভাবতে হবে। সন্তানকে তখন আমরা শেখাতে পারব সফলতা দুনিয়া কামাইয়ে নয়, মৃত্যুর পর অনন্ত জান্নাত হাছিলে।
‘সন্তানের শিক্ষা’ অর্থ এই না যে আমি তাকে অনেক তথ্য খালাম। বরং শিক্ষা হলো, আমার সন্তান বুঝতে শিখবে তার জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো দ্বীন। একজন সন্তান, যার হয়তোবা জ্ঞানের পরিমাণ কম, কিন্তু তার কাছে দ্বীন খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ, সে ওই সব সন্তান থেকে অনেক বেশি ভালো, যাদের জ্ঞান অনেক বেশি, যারা সবগুলো কুইজ প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয় এবং স্কুল-কলেজে পরীক্ষায় প্রথম হয় কিন্তু দ্বীনের কথা, আল্লাহর কথা, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কথা তার জীবনের প্রধান বিষয় নয়।
এটা নিজ সন্তানের ভেতরে কীভাবে আনা সম্ভব? সন্তানের আগে সবার প্রথমে নিজের জীবনে বাস্তবায়ন করার মাধ্যমে।
আপনার সন্তানের সাথে একটি গভীর সম্পর্ক গড়ে তুলুন। কাউকে দিয়ে পছন্দমতো কোনো কাজ করিয়ে নেবার পূর্বে আগে তার পছন্দসই মানুষ হতে হবে। আমাদের সমাজের ছেলেমেয়েদের জন্য সবচেয়ে বড় দ্বিধার জায়গা হলো, যে ব্যক্তি তার সন্তানের পরকালীন জীবন নিয়ে খুব বেশি চিন্তিত থাকে, সে তার সন্তানের প্রিয় ব্যক্তিত্ব না।
নিজ সন্তানের প্রিয় মানুষ হওয়া ব্যতীত আমি তাকে আল্লাহ ও দ্বীনের নিকটবর্তী করতে সক্ষম হব না। যে ব্যক্তি তার সন্তানের নিকট প্রিয় না এবং সে নিজে দ্বীনের উপর চলার চেষ্টা করছে, একটা ভয় আছে যে, সে নিজে তার সন্তানের দ্বীন থেকে দূরে সরে যাওয়ার কারণে পরিণত হতে পারে। আমাকে আমার সন্তানের প্রিয় ব্যক্তিত্ব হয়ে তাকে দ্বীনের পথে ডাকতে হবে।
অনেক মানুষ এ ধারণা নিয়ে বসে আছে যে, সন্তান প্রতিপালন অর্থ হচ্ছে অভিভাবককে অনেক বেশি টাকা আয় করতে হবে এবং সন্তান যখন যা চায় সে মনোকামনাগুলো পূরণ করতে হবে। অথচ আমাদের বোঝা উচিত বেশি সম্পদ সন্তানের উত্তম প্রতিপালনের ক্ষেত্রে যতটা না সহায়তা করে, অনেক ক্ষেত্রে তার চেয়ে বেশি প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। সন্তান প্রতিপালনের সর্বোত্তম মাধ্যমগুলো হলো ইলম, ন্যায়-নীতি, প্রজ্ঞা এবং ঈমানের শক্তি। আমাদের নিকট সন্তানের প্রধান দাবি আমাদের স্নেহ-ভালোবাসা, মনোযোগ এবং তাদের সাথে আমাদের সুসম্পর্ক।
শিক্ষা মনস্তত্ত্ববিদ এবং পরিচালক, এডুকেশনাল রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট সেন্টার, পাকিস্তান।
মূল (উর্দূ) : সালমান আসিফ ছিদ্দীক্বী
অনুবাদ ও পরিমার্জন : মুহাম্মাদ সাজিদ করিম
শিক্ষক, আল-জামি‘আহ আস-সালাফিয়্যাহ, ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী।