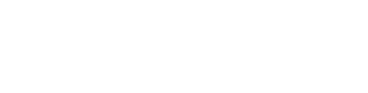ভূমিকা : স্কটল্যান্ডের গ্লাসগোতে গত ৩১ অক্টোবর থেকে শুরু হয়েছে বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলন (কপ-২৬)। যা ১২ নভেম্বর, ২০২১ পর্যন্ত চলছিল। প্যারিস চুক্তি পরবর্তী সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এই সম্মেলন আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় বড় ধরনের পরিবর্তন আনতে পারে বলে বিশেষজ্ঞরা ধারণা করছেন।*
জলবায়ু সম্মেলন (কপ) : জাতিসংঘের জলবায়ু সম্মেলন কপ-২৬ সামনে রেখে গত ৩০-১০-২০২১ (শনিবার) তারিখে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার দাবিতে স্কটল্যান্ডের গ্লাসগোতে বিক্ষোভ করেছেন শত শত মানুষ। পরদিন রোববারও বিশ্বনেতাদের প্রতি একই দাবি নিয়ে রাজপথে ছিলেন অনেক পরিবেশ অধিকারকর্মী।
জলবায়ুর পরিবর্তনজনিত বিপর্যয় থেকে পৃথিবীকে রক্ষায় পদক্ষেপ নিতে বিশ্বনেতাদের চাপে ফেলতে বিভিন্ন দেশের পরিবেশ আন্দোলনকর্মীরাও বিক্ষোভ-সমাবেশে যোগ দিয়েছিলেন। ঐ বিক্ষোভে যোগ দেন জলবায়ু পরিবর্তনবিষয়ক আন্দোলনে সাড়া জাগানো সুইডিশ পরিবেশকর্মী গ্রেটা থুনবার্গ।
আগের চেয়ে আরও পরিষ্কার যে, সবচেয়ে ক্ষতিকারক তাপমাত্রা এড়ানো মানে ২০৩০ সালের মধ্যে বিশ্বব্যাপী কার্বন নির্গমন অর্ধেক করা। কিন্তু কয়েক বছর আগেও যা ছিল অকল্পনীয়, তা এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি। অনেক দেশ ও প্রতিষ্ঠান এ শতকের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে কার্বন নির্গমন শুন্যে নামানোর প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে।
তবে কি গ্লাসগো সেই স্থান হতে যাচ্ছে, যেখান থেকে বিশ্ব একটি শূন্য-কার্বন নির্গমন ভবিষ্যতের দিকে এগোচ্ছে? প্রকৃতপক্ষে এটি কখনোই সম্ভব নয় যে, একটি একক সম্মেলন থেকে তা অর্জিত হতে পারে। ‘কপ’ মানে কনফারেন্স অব দ্য পার্টিজ। এটি জাতিসংঘের একটি উদ্যোগ। জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় সরকারের জন্য বিশেষভাবে কপ ঠিক করা হয়। বার্ষিক সম্মেলনের মাধ্যমে
সমষ্টিগতভাবে সমস্যা মোকাবিলা করার একমাত্র ফোরাম হয়ে গেছে এটি। কিন্তু এটি প্রায় ২০০ দেশের ঐকমত্য নিয়ে কাজ করে। এসব দেশের ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে।
তেল বা কয়লাসমৃদ্ধ অনেক দেশ জলবায়ু নিয়ে আলোচ্যসূচিতে সব সময় প্রতিকূলতা সৃষ্টি করে। তারা সবকিছুর গতি কমানোর চেষ্টা করে থাকে। কিন্তু দরিদ্র ও ঝুঁকিতে থাকা দেশগুলো তাদের অস্তিত্ব নিয়ে হুমকির মধ্যে পড়ে সাহায্যের জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে। ২০০৫ সালের সম্মেলন থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত একই চিত্র চোখে পড়ে। কপের বিরল সফলতা বলতে ২০১৫ সালের প্যারিস সম্মেলনকে ধরা যেতে পারে। জলবায়ু বিপর্যয় এড়াতে এসব দেশ ২০১৫ সালের প্যারিস চুক্তিতে বৈশ্বিক উষ্ণতা প্রাক-শিল্পায়ন যুগের চেয়ে ২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশি যাতে না বাড়ে, সে ব্যাপারে সম্মত হয়েছিল। এটাই প্যারিস চুক্তি। এই চুক্তির মানে হলো, ২০৫০ সালের মধ্যে কার্বন নিঃসরণ কার্যত শূন্যে নামিয়ে আনার জন্য দেশগুলো ব্যাপকভাবে নিঃসরণ কমাবে।
জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে ধোঁকাবাজি : অনেকে মনে করেন, জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে যে সংকট, তা আসলে বিজ্ঞানীদের ধোঁকাবাজি। আবার অনেকের ধারণা, সরকার জনগণের ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখতেই জলবায়ু পরিবর্তনের নামে ষড়যন্ত্র করছে। এসব গবেষণা, জরিপ ও বিশ্লেষণের ভিত্তিতে এএফপি বলছে, জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য মানুষ দায়ী, এটি পুরোপুরি সত্য।
অনেকেই মনে করেন, জলবায়ুর বদল খুব স্বাভাবিক। প্রকৃতির নিয়মেই জলবায়ুতে বদল আসে। কিন্তু বিষয়টি এত সরল নয়। গত ৫০ বছরে প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মের তুলনায় দ্রুত বৈশ্বিক তাপমাত্রা বেড়েছে। আইপিসিসি বলছে, ১৯৭০ সাল থেকে ভূপৃষ্ঠের তাপমাত্রা দ্রুত বাড়ছে। শিল্পবিপ্লবের আগের সময় এবং ১৮৫০ সালের রেকর্ড করা তাপমাত্রার ভিত্তিতে এ ধরনের তথ্য দিয়েছে আইপিসিসি। এ সময়ের পলি, বরফ, গাছপালার যৌগিক বিশ্লেষণও করেছে আইপিসিসি।
অনেকে বিশ্বাস করেন, পৃথিবীর তাপমাত্রা অস্বাভাবিক হারে বাড়ছে। তবে জীবাশ্ম জ্বালানি পুড়িয়ে মানুষ কার্বন নির্গমন বাড়ানোর কারণেই যে এমনটা ঘটছে, তা অনেকে মানতে চান না। আইপিসিসি জলবায়ু পরিবর্তনের একটি মডেল নিয়ে কাজ করছে। বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধিতে কোন কোন বিষয় প্রভাব ফেলছে, তা বিশ্লেষণ করা হয়েছে এ মডেলে। এ বছর আইপিসিসির প্রতিবেদনে জানানো হয়, বায়ুমণ্ডল, সাগর ও ভূপৃষ্ঠের উষ্ণতা বৃদ্ধির জন্য নিঃসন্দেহে মানুষই দায়ী।
বিশ্বের অনেক দেশেই তীব্র শীত। এসব দেশে প্রচুর তুষারপাত হয়। এসব অঞ্চলের মানুষ মনে করে, বৈশ্বিক উষ্ণতা কিছুটা বাড়া খারাপ নয়। বিজ্ঞানীরা বলছেন, বিভিন্ন সময়ে আবহাওয়ার গড় ওঠানামা অনুসারে জলবায়ু পরিবর্তন পরিমাপের মাপকাঠি। এক দিন অথবা এক সপ্তাহ তুষারপাত হলেই কয়েক দশক ধরে গড় উষ্ণতা বাড়েনি, এমনটা প্রমাণ হয় না।
বৈশ্বিক উষ্ণতা কিছুটা বাড়লে কী হতে পারে? সাইবেরিয়ার কিছু অংশ চাষযোগ্য হতে পারে। খাদ্যের জোগান দিতে পারে। তবে উষ্ণতা বেড়ে যাওয়ার কারণে এসব অঞ্চলের বরফ গলে আরও বড় সংকট তৈরি হতে পারে। আইপিসিসির বিজ্ঞানীরা বলছেন, দুই ডিগ্রি তাপমাত্রা বাড়লেও সাগরের উচ্চতা আধা মিটার বা তারও বেশি বাড়তে পারে। এর প্রভাবে উপকূলবর্তী শহরগুলো ডুবেও যেতে পারে।
জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে নানা যৌথ বিবৃতি আসে। তবে বিশ্লেষণের পর দেখা গেছে, তাঁদের মধ্যে খুব কমই জলবায়ুবিজ্ঞানী। জলবায়ু পরিবর্তন ইস্যুতে বিজ্ঞানী ও গবেষকদের মধ্যে ঐকমত্য থাকাটা খুব জরুরী। জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে কর্নেল ইউনিভার্সিটিতে কয়েক হাজার জরিপ ও গবেষণা পরিচালিত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়টি বলছে, জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য যে মানুষ দায়ী, এ ব্যাপারে ৯৯ শতাংশের বেশি বিজ্ঞানী একমত পোষণ করেছেন।
বিজ্ঞানীদের সতর্কতা ও বিশ্ব নেতাদের ব্যর্থতা : দাবদাহ, দাবানল ও বন্যার মতো জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট চরমভাবাপন্ন আবহাওয়া তীব্রতর হচ্ছে। গত দশক ছিল রেকর্ড গরম। বিজ্ঞানীরা বারবার এ ব্যাপারে সতর্কতা উচ্চারণ করে আসছেন। বিশ্বের সরকারগুলো একমত যে, এ বিষয়ে জরুরী ভিত্তিতে যৌথ পদক্ষেপ দরকার।
কপ-২৬ সম্মেলনে বিশ্বের ২০০টি দেশের কাছে ২০৩০ সালের মধ্যে কার্বন নিঃসরণ কমানোর বিষয়ে তাদের পরিকল্পনা জানতে চাওয়া হয়েছে। জলবায়ু বিপর্যয় এড়াতে এই দেশগুলো ২০১৫ সালের প্যারিস চুক্তিতে বৈশ্বিক উষ্ণতা প্রাকশিল্পায়ন যুগের চেয়ে ২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশি যাতে না বাড়ে, সে ব্যাপারে সম্মত হয়েছিল। তবে এরই মধ্যে বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে, বৈশ্বিক তাপমাত্রার বৃদ্ধি ১.৫ ডিগ্রিতে সীমিত না রাখতে পারলে বিপর্যয় এড়ানো যাবে না।
কপ-২৬–এর সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণকারী অলোক শর্মা ঘোষণা দিয়েছেন, প্যারিস যেখানে অঙ্গীকার করেছিল, গ্লাসগো সেখানে তা পূরণ করবে। তবে চুক্তির লক্ষ্য অর্জনে শীর্ষ দূষণকারী শিল্পোন্নত দেশগুলো কতটা পদক্ষেপ নিতে প্রস্তুত, সবার নজর আসলে সেই জি-২০–এর রোম শীর্ষ সম্মেলনের সমঝোতার দিকে।
জি-২০–এর নেতারা চলতি শতকের শেষে বিশ্বের তাপমাত্রা বৃদ্ধির হার দেড় ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে সীমিত রাখার লক্ষ্যের প্রতি তাঁদের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেছেন। তবে তা অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় কী কী পদক্ষেপ তাঁরা গ্রহণ করবেন, তার সামান্যই প্রকাশ করা হয়েছে। বিশেষ করে ২০৫০ সালের মধ্যে নেট জিরো বা যতটা ক্ষতিকর গ্যাস নির্গমন হচ্ছে, ততটাই বায়ুমণ্ডল থেকে অপসারণের বিষয়ে অস্পষ্টতা রয়ে গেছে।
এবারের জলবায়ু সম্মেলনকে (কপ-২৬) খুব বেশি আশাব্যঞ্জক মনে করা হচ্ছে না। এর সহজ কারণ, আগের সম্মেলনগুলোর ব্যর্থতা। আগের ২৫টি বড় সম্মেলনের পরও বিশ্বে গ্রিনহাউস গ্যাসের নির্গমন ঠেকিয়ে বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধি ঠেকানো সম্ভব হয়নি। তিন দশক ধরে আলোচনার পরও শিল্পপূর্ব যুগের তুলনায় বিশ্ব ১.১ ডিগ্রি বেশি উষ্ণ। এ উষ্ণতা ক্রমেই বাড়ছে। এর আগে যে ২৫টি সম্মেলন হয়েছে তাতে খুব একটা সুফল পাওয়া গেছে, এমন নয়। নেতারা আলোচনা করেছেন, রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব থেকে ক্ষণিকের ছুটি নিয়ে বিলাসবহুল সম্মেলনস্থলে কিছুটা হাত-পা মেলে অবকাশ যাপন করেছেন এবং নিজ দেশে ফিরে নব উদ্যমে আগের কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়েছেন। সম্মেলনের কথা হয়তো ভুলেই গেছেন। ফলে ওই সম্মেলনগুলোকে অনেকে বিশ্ব নেতাদের বার্ষিক বনভোজন বলতেও দ্বিধা করেননি।
বিশ্বের সবচেয়ে কার্বন নিঃসরণকারী দেশ চীন এবং যুক্তরাষ্ট্র কার্বন ডাই অক্সাইড নির্গমন কমানোর লক্ষ্য পূরণের জন্য লড়াই করে যাচ্ছে। এই জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সবচেয়ে ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে দরিদ্র দেশগুলো। তাদের জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে সাহায্য করার জন্য দরিদ্র দেশগুলোকে গ্রিন টেকনোলজি বা পরিবেশ বান্ধব প্রযুক্তি দেয়ার প্রতিশ্রুতি করেছিল ধনী দেশগুলো। কিন্তু এ জন্য যে অর্থ প্রয়োজন ছিল, এই ধনী দেশগুলো তা দিতে ব্যর্থ হয়েছে।
উপসংহার : সবাই নির্গমন কমাতে তাদের বর্তমান প্রতিশ্রুতিতে অটল থাকলেও এ শতকের শেষ নাগাদ বিশ্বে তাপামাত্রা বৃদ্ধি ২.৭ ডিগ্রির বিপজ্জনক পথেই থাকবে। তাই এবারের সম্মেলন ঘিরে প্রকৃত অগ্রগতির প্রত্যাশা স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি। এর আংশিক কারণ, ঝুঁকি এখন ঘরে উঠে আসতে শুরু করেছে। এ বছরের বন্যায় জার্মানিতে ২০০ জনের প্রাণহানি ঘটেছে। শীতল কানাডায়ও তীব্র তাপদাহ দেখা গেছে। এমনকি সাইবেরিয়ার উত্তর মেরুও পুড়তে দেখা গেছে। তাই প্রশ্ন উঠেছে, বৈশ্বিক তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে এবারের সম্মেলনের কি আদৌ কোনো ভূমিকা আছে?