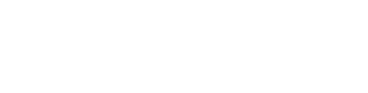(মিন্নাতুল বারী- ৯ম পর্ব)
উম্মুল মুমিনীন বলতে কাকে বুঝায়?
মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেন, النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ ‘নবী মুমিনদের নিজেদের চেয়ে তাদের বেশি ঘনিষ্ঠ আর নবীর স্ত্রীগণ তাদের মা’ (আহযাব, ৬)।
উক্ত আয়াতে মহান আল্লাহ তাদেরকে আমাদের মা হিসাবে ঘোষণা করেছেন। তবে আমাদেরকে মনে রাখতে হবে যে, তাদের এই মাতৃত্ব শুধুমাত্র সম্মান ও বিবাহ হারাম হওয়ার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, অন্য কোনো ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। যেমন আমাদের নিজেদের মায়েদের জন্য আমরা মাহরাম, কিন্তু রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর স্ত্রীগণ আমাদের মা হলেও তাদের জন্য আমরা মাহরাম নই। ফলে, তাদের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করা বা তাদের সাথে সফর করা আমাদের জন্য জায়েয নেই। ঠিক তেমনি আমাদের নিজ মায়ের মেয়ে তথা আমদের বোনদের সাথে আমাদের বিবাহ হারাম হলেও উম্মাহাতুল মুমিনীনের কন্যাদের সাথে আমাদের বিবাহ জায়েয। সুতরাং তারা আমাদের মা শুধুমাত্র সম্মান ও বিবাহ হারাম হওয়ার ক্ষেত্রে; অন্য কোনো ক্ষেত্রে নয়।
রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে মুমিনগণের পিতা বলা যাবে কি?
যেভাবে রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর স্ত্রীগণকে মুমিনগণের মাতা বলা হয়েছে, ঠিক সেভাবে রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে কি মুমিনগণের পিতা বলা যাবে? এ ব্যাপারে বিশুদ্ধ মত হচ্ছে, হ্যাঁ, বলা যাবে। দলীলসমূহ নিমেণ পেশ করা হলো:
عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ بِمَنْزِلَةِ الْوَالِدِ أُعَلِّمُكُمْ
আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘নিশ্চয় আমি তোমাদের পিতার মতো। এজন্য আমি তোমাদের (সবকিছুই) শিক্ষা দিই (এমনকি পেশাব পায়খানার নিয়মও)’।[1]
কিন্তু এখানে প্রশ্ন আসতে পারে যে, মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেছেন,مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ‘মুহাম্মাদ তোমাদের কোনো ব্যক্তির পিতা নন, বরং তিনি মহান আল্লাহর রাসূল ও সর্বশেষ নবী’ (আহযাব, ৪০)।
উক্ত আয়াতের জবাব হচ্ছে, এখানে মহান আল্লাহ ঔরসজাত সন্তানের পিতা হওয়ার কথাকে নাকচ করেছেন। কিন্তু সম্মানসূচকভাবে তিনি সকল মুমিনের পিতার স্থানে, যেমনটা তিনি হাদীছে বলেছেন।
হারিছ ইবনে হিশাম রাযিয়াল্লাহু আনহু: তিনি ছহীহ বুখারীর আলোচ্য ২য় হাদীছের মূল জিজ্ঞাসাকারী। তিনি আবু জাহলের সহোদর ভাই। বদরের যুদ্ধে মুসলিমদের বিরুদ্ধে ও কাফেরদের পক্ষে লড়াই করেছিলেন। মক্কা বিজয়ের সময় তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। ইয়ারমুকের যুদ্ধে তিনি শাহাদাত বরণ করেন।[2]
হাদীছটি আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা-এর বর্ণিত নাকি হারিছ ইবনে হিশাম রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর?:
হাদীছটিতে মূলত প্রশ্নকারী হচ্ছেন হারিছ ইবনে হিশাম। যদি তার এই প্রশ্ন করার সময় স্বয়ং আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা উপস্থিত থেকে থাকেন এবং পর্দার আড়াল থেকে রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উত্তর শুনে থাকেন, তাহলে এই হাদীছটি আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা-এর মাসানীদ তথা তার বর্ণিত বর্ণনা বলে গণ্য হবে। অন্যদিকে যদি তিনি উপস্থিত না থাকেন, বরং পরবর্তীতে হারিছ ইবনে হিশাম থেকে এই ঘটনা শুনে থাকেন, তাহলে হাদীছটি হারিছ ইবনে হিশামের মাসানীদ তথা তার বর্ণিত হাদীছ বলে গণ্য হবে। মুসনাদে আহমাদে একটি বর্ণনা পাওয়া যায়, যেখানে স্পষ্টভাবে এটিকে হারিছ ইবনে হিশামের বর্ণনা হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে।[3] কিন্তু কোনো মুহাদ্দিছই এটিকে গ্রহণ করেননি। কেননা সেই বর্ণনার সূত্রে একজন দুর্বল রাবী আছেন, যার নাম আমীর ইবনে ছালেহ। হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী তাকে মাতরূক বা পরিত্যক্ত বলেছেন।[4] এজন্য সকল মুহাদ্দিছই এটিকে আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা-এর মাসানিদের অন্তর্ভুক্ত গণ্য করেছেন। যার জ্বলন্ত প্রমাণ ‘আতরাফ’-এর গ্রন্থগুলো। প্রায় সব আতরাফের গ্রন্থে হাদীছটিকে আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা-এর মুসনাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।[5]
সনদের সূক্ষ্মতা :
(ক) হাদীছটি মাদানী সনদের হাদীছ। এই সনদের সকল রাবী মদীনার অধিবাসী, শুধুমাত্র একজন ব্যতীত, তিনি হচ্ছেন আব্দুল্লাহ ইবনে ইউসুফ আত-তিন্নিসী। তিনি জন্মগতভাবে সিরিয়ার অধিবাসী এবং মিশরে মারা গেছেন।[6]
(খ) উক্ত হাদীছে দু’জন তাবেঈ একজন আরেকজন থেকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন। হিশাম ইবনে উরওয়া তাবেঈ আবার তিনি যার থেকে হাদীছ শুনেছেন উরওয়া ইবনে যুবায়েরও তাবেঈ।
(গ) উক্ত হাদীছে পরপর তিনজন রাবী পরস্পরের আত্মীয়। ছেলে হিশাম পিতা উরওয়া থেকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন। পিতা উরওয়া তার খালা আয়েশা থেকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন।
(ঘ) হাদীছটি যদি হারিছ ইবনে হিশামের হয়ে থাকে এবং তার জিজ্ঞাসার সময় যদি আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা উপস্থিত না থেকে থাকেন, তাহলে এটি মুরসাল ছাহাবীর অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে।
উল্লেখ্য, ‘মুরসালুছ-ছাহাবী’ বলা হয় সেই সব হাদীছকে, যেগুলো এক ছাহাবী অন্য ছাহাবী থেকে বর্ণনা করে থাকেন। বিশেষ করে ছোট বয়সী ছাহাবীদের এই রকম বর্ণনা অনেক আছে। যেমন আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মৃত্যুর মাত্র চার বছর আগে ইসলাম গ্রহণ করেছেন।[7] আব্দুল্লাহ ইবনে আববাস রাযিয়াল্লাহু আনহু অনেক ছোট ছিলেন। এজন্য রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রাথমিক জীবনের অনেক ঘটনা তারা বড় বড় ছাহাবী থেকে শুনে বর্ণনা করেছেন। আবার অনেক সময় নিজস্ব পারিবারিক, ব্যক্তিগত ও পেশাগত কাজের জন্য সব মজলিসে সব সময় সব ছাহাবীর উপস্থিত থাকা হয় না। তখন মজলিসে অনুপস্থিত থাকা ছাহাবীগণ উপস্থিত ছাহাবীগণ থেকে সেই মজলিসের হাদীছগুলো শুনে নেন। এই বিষয়ে ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর বর্ণিত স্পষ্ট হাদীছ আছে।
عَنْ عُمَرَ، قَالَ: كُنْتُ أَنَا وَجَارٌ لِي مِنَ الأَنْصَارِ فِي بَنِي أُمَيَّةَ بْنِ زَيْدٍ وَهِيَ مِنْ عَوَالِي المَدِينَةِ وَكُنَّا نَتَنَاوَبُ النُّزُولَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَنْزِلُ يَوْمًا وَأَنْزِلُ يَوْمًا، فَإِذَا نَزَلْتُ جِئْتُهُ بِخَبَرِ ذَلِكَ اليَوْمِ مِنَ الوَحْيِ وَغَيْرِهِ، وَإِذَا نَزَلَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ
ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমার একজন আনছার প্রতিবেশী ছিল, সে মদীনার আওয়ালী অঞ্চলের। আমরা দু’জনে পালা করে রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকটে যেতাম। যেদিন আমার পালা থাকত, সেদিন আমি রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দারসের অহিসহ আর যা কথা থাকত সব এসে তাকে বলতাম। ঠিক তেমনি তার যেদিন পালা থাকত, সেদিন সেও আমাকে এসে সব বলত।[8]
এভাবে এক ছাহাবী থেকে আরেক ছাহাবীর বর্ণিত হাদীছকে ‘মুরসালুছ-ছাহাবী’ বলা হয়। মুরসালুছ-ছাহাবী মুহাদ্দিছগণের নিকট গ্রহণযোগ্য। কেননা সকল ছাহাবী ন্যায়পরায়ণ ও মযবূত। সনদে ছাহাবীর উল্লেখ না থাকাটা সনদের জন্য ত্রুটি নয়। কেউ অভিযোগ করতে পারেন, হতে তো পারে যে সেই ছাহাবী হাদীছটি অন্য ছাহাবী থেকে না শুনে অন্য কোনো তাবেঈ থেকে শুনেছেন। এর জবাবে হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী রাহিমাহুল্লাহ একটি বই লিখেছেন। যেখানে তিনি ছাহাবীগণের ঐ সমস্ত বর্ণনাকে সংকলন করার চেষ্টা করেছেন, যেগুলো তারা তাবেঈ থেকে বর্ণনা করেছেন। তার গবেষণায় যা দেখা গেছে, এই রকম বর্ণনার সংখ্যা সর্বোচ্চ ত্রিশটি, তাও আবার তার অধিকাংশই দুর্বল। তার লিখিত পুস্তিকাটির নাম ‘নুযহাতুস সামি‘ঈন ফী রিওয়াতিছ ছাহাবা আনিত তাবেঈন’। সুতরাং মুরসালুছ-ছাহাবী হুজ্জাত বা দলীল হওয়া নিয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশ থাকে না।
কঠিন ও অপরিচিত শব্দের অর্থ :
صَلْصَلَةُ (ছলছলা): শব্দটির শাব্দিক অর্থ,صَوْتُ وُقُوعِ الْحَدِيدِ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ ‘একটা লোহা আরেকটা লোহার উপর পড়লে যে শব্দ তৈরি হয়, তাকে ছলছলা বলা হয়। এমনটিই বলেছেন ইবনুল আছীরসহ অন্যান্য ভাষাবিদ।[9] ইমাম সূয়ূতী বলেন, ‘এটি মূল অর্থ হলেও প্রত্যেক যে শব্দ পরস্পর চলতে থাকে বাজনার মতো, তার ক্ষেত্রে ছলছলা শব্দটি প্রয়োগ করা হয়ে থাকে’।[10]
جَرَسٌ(জারাস): ইমাম ইবনুল আছীর তার আন-নিহায়া গ্রন্থে বলেন, الْجُلْجُلُ الَّذِي يعلق فِي رُؤُوس الدَّوَابِّ ‘প্রাণীদের মাথায় বা গলায় ঝুলানো হয় যে ছোট ঘণ্টা, তাকেই জারাস বলা হয়’।[11] ড. আহমাদ মুখতার বলেন,
أَدَاةٌ من نُحَاسٍ أَو نحوه ، مجوّفة ، إِذا حُرَّكَتْ تَتَذَبْذَبُ فيها قطعةٌ صغيرةٌ صُلْبَةٌ ، فيُسْمَعُ صوتُها
‘জারাস হচ্ছে তামার তৈরি গোলাকার একটি বস্ত্ত, যার মধ্যে ছোট একটি ঘণ্টা থাকে। যখন সেই গোলাকার তামাটি নড়ে তখন তার মাঝে থাকা ঘণ্টাটি তার মাঝে হেলতে দুলতে থাকে এবং শব্দ হয়’।[12]
فَيُفْصَمُ (ইউফছামু): শব্দটি মুযারে‘ মাজহূলের ওয়াহেদ মুযাক্কার গায়েবের ছীগাহ। তথা ভবিষ্যতকালের অর্থ প্রদানকারী কর্মবাচক ক্রিয়া। ক্রিয়াটি একবচন নাম পুরুষ ক্রিয়া। ক্রিয়াটি বাবে ‘যরাবা’ থেকে। শব্দটির অর্থ বলতে গিয়ে ক্বাজী ইয়ায বলেছেন,والفصم -بالفاء-: القطع من غير بينونة ‘কোনো কিছুর এমনভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া, যে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পরও তার প্রভাব বাকী থাকে। সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হওয়া নয়’। তাহলে অর্থ দাঁড়ায় ‘আমার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়’। এই শব্দে যে সর্বনামটি গোপন আছে তা অহি অথবা ফেরেশতা। তাহলে বাক্যটির অর্থ দাঁড়ায়, যখন অহি আমার থেকে বিচ্ছিন্ন হয় বা ফেরেশতা আমার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়।[13]
উল্লেখ্য, অন্য বর্ণনায় ক্রিয়াটি বাবে ‘ইফ‘আল’ থেকে মা‘রূফের ছীগাহ হিসাবে এসেছে। তথা- يُفصِمُ ইয়াতে পেশ ও ছোয়াদে যের দিয়ে। যখন বৃষ্টি থেমে যায়, তখন আরবে বলে থাকে, أَفْصَمَ المطَرُ ‘বৃষ্টি থেমে গেল’। বাবে ইফ‘আল থেকে শব্দটির অর্থ হচ্ছে, থামা। তবে এই শব্দটি এভাবে আরবী ভাষায় অনেক কম ব্যবহৃত হয়। সেই হিসাবে প্রথমটি তথা বাবে ‘যরাবা’ থেকে বেশি বিশুদ্ধ।[14]
وَعَيْتُ (ওয়া‘আয়তু): মাযী মা‘রূফ ওয়াহিদ মুতাকাল্লিমের ছীগাহ। তথা অতীতকালের অর্থ প্রদানকারী কর্তৃবাচক ক্রিয়া। ক্রিয়াটি একবচনবিশিষ্ট উত্তম পুরুষ। ক্রিয়াটি ‘সামি‘আ’ বাব থেকে। যার শাব্দিক অর্থ- সংরক্ষণ করা বা মুখস্থ করা। তাহলে অর্থ দাঁড়াল, ‘আমি তার থেকে অহি মুখস্থ করে নিই বা সংরক্ষণ করে নিই’।
أَحْيَانًا (আহইয়ানান): যর্ফ হওয়ার কারণে এটি যবরবিশিষ্ট হয়েছে। শব্দটি বহুবচন, যার একবচন হচ্ছে, حِين (হিন)। ‘হিন’ শব্দটির অর্থ হচ্ছে, সময়। যেমন মহান আল্লাহ বলেন, هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ ‘মানুষের উপর এমনও সময় গেছে, যখন সে কিছুই ছিল না’ (দাহ্র, ১)। অতএব ‘আহইয়ান’ শব্দের অর্থ হচ্ছে, কখনো কখনো।
جَبِينَه (জাবীন): শব্দটির অর্থ বর্ণনা করতে গিয়ে ইমাম দামামিনী বলেন,
والجبين غير الجبهة وهو فوق الصدغ والصدغ ما بين العين والأُذن، فللإنسان جبينان يكتنفان الجبهة، والمراد والله أعلم أن جبينيه معًا يتفصدان. فإن قلت: فلم أفرده؟ أجيب: بأن الإفراد يجوز أن يعاقب التثنية في كل اثنين يغني أحدهما عن الآخر كالعينين والأُذنين. تقول: عينه حسنة وأنت تريد أن عينيه جميعًا حسنتان
‘জাবীন দ্বারা কপাল উদ্দেশ্য নয়। বরং ছুদগের উপরের জায়গাকে জাবীন বলা হয়। আর ছুদগ বলা হয় কান ও চোখের মাঝামাঝি জায়গাকে। আর প্রত্যেক মানুষের কপাল লাগোয়া দুই ধারে দুটি জাবীন আছে। তাহলে অর্থ দাঁড়ায়, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কপালের দুই পার্শ্ব দিয়ে ঘাম ঝরত। প্রশ্ন আসতে পারে, তাহলে ‘জাবীন’-কে একবচন কেন ব্যবহার করা হলো? জবাবে বলব, আরবী ভাষায় এমন দ্বি-বচন বিশেষ্যের ক্ষেত্রে একবচন ক্রিয়া ব্যবহার করা যায়, যে দ্বি-বচন বিশেষ্যটি একটা আরেকটা থেকে অবিচ্ছেদ্য। যাদের কখনই একবচন হওয়ার সুযোগ নেই। যেমন দুই কান, দুই চোখ। সেই হিসাবে কেউ যদি বলে, ‘তার চোখ সুন্দর’ তাহলে উদ্দেশ্য হয় তার চোখ দুটি সুন্দর’।[15]
لَيَتَفَصَّدُ (লাইয়াতাফাছছাদু) : লামটি এখানে তাকীদ তথা গুরুত্ব বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। এটি ভবিষ্যত অর্থ প্রদানকারী কর্তৃবাচক ক্রিয়া। ক্রিয়াটি একবচনবিশিষ্ট নাম পুরুষ। বাবে তাফাঊল থেকে। শব্দটির অর্থ হচ্ছে, প্রবাহিত হওয়া বা বয়ে যাওয়।
عَرَقًا (‘আরাক্ব): শব্দটি যবরবিশিষ্ট হয়েছে তাময়ীয হওয়ার কারণে। শব্দটির অর্থ, ঘাম।
[1]. আবুদাঊদ, হা/৮।
[2]. সিয়ারু আলামিন নুবালা, ৪/৪২০।
[3]. মুসনাদে আহমাদ, হা/২৫২৫৩।
[4]. তাকরীবুত তাহযীব, রাবী নং-৩০৯৬।
[5]. ইমাম মিযযী, তুহফাতুল আশরাফ, হা/১৭১৫২, ১৭১৮৭।
[6]. তারীখুল কাবীর, ৫/২৩৩; তারীখুল ইসলাম, ৫/৩৬২।
[7]. আল-ইসাবা, ৭/৩৪৮।
[8]. ছহীহ বুখারী, হা/৮৯।
[9].আন-নিহায়া ফী গরীবিল হাদীছ, ৩/৪৬; আবুবকর আল-আযদী, জামহারাতুল লুগাহ, ১/২০৯।
[10]. সূয়ূতী, তাওশীহ, ১/১২১।
[11]. আন-নিহায়া, ১/২৬১।
[12]. মু‘জামুল লুগাহ আল-আরাবিয়্যাহ, ১/৩৬৩।
[13]. দামামিনি, মাছাবিহুল জামে‘, ১/৬।
[14]. প্রাগুক্ত।
[15]. প্রাগুক্ত।